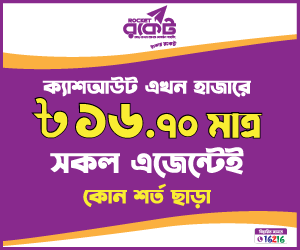প্রতিদিনই আমাদের ঘরে বা ঘরের আশপাশের দেয়ালে বা ঝোপ-ঝাড়ে, ফুল ও ফলের বাগানে বা ফসলের জমিতে বিশেষ ধরনের বন্যপ্রাণীর নিঃশব্দ বিচরণ সহজেই চোখে পড়ে। আমাদের আনন্দের খোরাক যোগায়। এরা সবজি বাগানের লতায় পাতায় ঘুরে ঘুরে লম্বা জিহ্বা ছুড়ে দিয়ে পোকা মাকড় ধরে খায় আবার কখনো টিকটিক শব্দ করে দুপুর কিংবা নিঃসঙ্গ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রকৃতির প্রতি আমাদেরকে অনুরাগী করে তোলে। তারা হলো টিকটিকি জাতীয় বন্যপ্রাণী যেমন-রক্ত চোষা, ড্রাকো, তক্ষক বা সান্ডা, আঞ্জন বা আঁচিলা ও গুই ইত্যাদি। এদের কেউ কেউ বনে বাস না করলেও মানুষের যত্নছাড়া প্রকৃতিতে বেঁচে থাকায় তাদেরকে বন্যপ্রাণী বলে।
বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীতে ৩ হাজার ৩০০ প্রজাতিরও বেশি টিকটিকি ও গিরগিটি জাতীয় প্রাণী রয়েছে। প্রাণী বিজ্ঞানী ড. রেজা খান এবং এস ইউ সরকারের মতে বাংলাদেশে ৩২ প্রজাতির টিকটিকি জাতীয় প্রাণী দেখা যায়। যেমন-খসখসে টিকটিকি, মসৃণ টিকটিকি, গোদা টিকটিকি, দেয়াল টিকটিকি, গেছো টিকটিকি, ছোট টিকটিকি, রক্তচোষা বা কাকলাস, তক্ষক বা সান্ডা, আঞ্জন বা আচিঁলা, গুইল বা গুইসাপ ইত্যাদি। এরা বাড়ির আঙিনায় ফলানো ফল-ফুল বা সবজি বাগানে যেমন-লাউ, কুমড়া, শসা, চিচিঙ্গা, ঝিঙা, বরবটি, ভেন্ডি, পটল, কাকরল, ডাটা শাক, পুঁইশাক, পালংশাক প্রভৃতি ফসলের জমির ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায়। তাছাড়া ঘর বাড়ির পরিবেশ কীটপতঙ্গ খেয়ে পরিচ্ছন্ন রাখে।
আমাদের দেশের সর্বত্র বিশেষ করে মানুষের বসতবাড়িতে, পেট্রোল পাম্পে, গাছ-গাছালি ও ঝোপঝাড়ে, বাগানের গাছে, আর্দ্র এলাকায়, বিদ্যুতের খুটিতে, জলাভূমি, ফসলের জমিতে, গাছের ডালে ডালে টিকটিকি জাতীয় বন্যপ্রাণীদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। বসতবাড়িতে বাস করা টিকটিকিরা দিনের বেলায় বাথরুমে, আলমিরা, বুকশেলফ, মিটসেফ, পর্দার আড়ালে, বেসিনে এবং ঘরের বিভিন্ন জায়গায় খানিকটা অন্ধকার জায়গায় লুকিয়ে থাকে এবং টিক টিক করে ডাকে। রাতে খাবারের জন্য এরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে এদের আনাগোনা অনেকটা বেড়ে যায়। ঘরের ফাঁক ফোকড়ে, এমনকি আলমিরা, সেলফ, কাপড়ের ফাঁকে ও ঘরের বিভিন্ন জায়গায় এরা ডিম পাড়ে। ডিমগুলো দেখতে সাদা এবং ডিম্বাকার। কোনোরকম তা দেয়া ছাড়াই ৪০-৫০ দিনের মধ্যে ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে আসে। টিকটিকি দেখলেই মানুষ বিনা কারণে ভয় পায় এবং মারার জন্য আঘাত করে। ফলশ্রুতিতে নিরাপরাধ পরোপকারী টিকটিকির সংখ্যা দিনদিন কমছে।
গিরগিটি গোত্রের অন্যতম প্রজাতি হচ্ছে রক্তচোষা বা কাকলাস যা দেশের সর্বত্রই দেখা যায়। গিরগিটি নামটি বইপুস্তকে বেশি ব্যবহার করা হয়। শিকারী প্রাণীর আগমনে নিজেদের বাঁচানোর জন্য বা ভয় পেলে রক্তচোষার দেহের রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায় ফলে তাদের দেহের কিছু অংশ লালচে বর্ণ ধারণ করে, লোকজন মনে করেন, রক্তচোষা মানুষের দেহ থেকে রক্ত শুষে নিচ্ছে। তাই রক্তচোষার দেহ লাল হচ্ছে। আসলে ব্যাপারটি অন্য রকম। রক্তচোষার শরীরের ওপরের স্তরে নানা বর্ণের শুষ্ক কোষ আছে। বিভিন্ন বর্ণচ্ছটা ক্রোমাটোফোরও থাকতে পারে। রঞ্জক-কোষ এবং ক্রোমাটোফোরের স্থানান্তরের কারণে রক্তচোষার গায়ের রঙের হেরফের হয়।
বিজ্ঞানীরা মনে করেন শিকারী বা শত্রুর সামনে পড়লে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে দেহের রঙ পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজের চেহারাকে কিছুটা ভয়াল করার ভেতর দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে পাশাপাশি বাস করা দুটো পুরুষ রক্তচোষাকে দৈহিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় না। দেহের রঙ পরিবর্তনের ফলে দেহে তাপ নিয়ন্ত্রণেরও সুবিধা হয়। উপরন্তু মেয়ে রক্তচোষার পক্ষে পুরুষ রক্তচোষা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। অনেক সময় মানুষের সামনে পড়লে ভয় পেলেও তাদের দেহ-বর্ণের পরিবর্তন হতে পারে। রক্ত শুষে খাবার ভ্রান্ত ধারণা সাধারণ মানুষ যুগযুগ ধরে পোষণ করে আসছে এর ফলে জীবন দিতে হচ্ছে হাজারো নিরীহ রক্তচোষাকে। এরা মে থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে মাটি খুঁড়ে ১০ থেকে ২৫টির মতো ডিম পাড়ে। মা-বাবার যত্ন ছাড়াই ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে আসে। আমাদের দেশে ১০ ধরনের রক্তচোষা দেখা যায়।
আঞ্জন বাংলাদেশের সর্বত্রই বনে-জঙ্গলে, বাড়িঘরের আশেপাশে বিচরণ করতে দেখা যায়। স্থানীয় ভাষায় এদেরকে আঁচিল বলে। টিকটিকিদের চেয়ে আঞ্জনদের আঁইশ অপেক্ষাকৃত ছোট এবং সবসময় একটি আঁইশ অন্যটির ওপর দিয়ে এমনভাবে উঠে থাকে, দূর থেকে দেখলে গা মসৃণ মনে হয় এবং গা চিক চিক করে। এদের পা অপেক্ষাকৃত ছোট। এরা শুকনো পাতার নিচে, গাছের গুঁড়িতে, রাস্তার দুইধারে ছোটছোট ঝোপঝাড়ের মধ্যে, কখনো জলাশয়ে ভাসমান উদ্ভিদের ওপর খাবার ধরার জন্য ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এরা বেশিরভাগ সময় জলাশয়ের আশেপাশে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় পোকামাকড় ধরার জন্য ঘোরাফেরা করে। আমাদের দেশে ৫ ধরনের আঞ্জন দেখা যায়।
তক্ষক বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কমবেশি দেখা যায়। পাহাড়ি অঞ্চলের বনভূমিতে পুরাতন গাছে, বসতবাড়ির কার্নিসে, দালানের বা পুরাতন গাছের ফাঁক ফোকরে, কাঠের ও ছনের ঘরে এবং বিভিন্ন আসবাবপত্রের ফাঁকে নির্জন আলো-আঁধারে তাদের বেশি দেখা যায়।
শহর থেকে শুরু করে গ্রামীণ পরিবেশের সর্বত্রই তক্ষক দেখা যায়। একই বসতিতে বছরের পর বছর দখল করে থাকে একজোড়া তক্ষক। দিনের বেলা তারা গর্তের মুখে এসে মাথাটা বাইরের দিকে বের করে থাকে। পরিচিত গর্তের মুখে এদেরকে রোজই দেখা সম্ভব। খুব অল্প লোকে তক্ষক দেখেছেন। তবে ডাক শুনেছেন প্রায় লোকই। তক্ষক তঙ্ক-তঙ্ক বা টোকা ঢোকে অথবা গেক্কো-গেক্কো শব্দ করে বেশ জোরে জোরে ডাকে। ডাক শুনেই তক্ষকের উপস্থিতি বোঝা যায়। বিশেষ করে স্ত্রী-পুরুষের যোগাযোগের জন্য বা বাসস্থানের দখল বজায় রাখার জন্য ডাকাডাকি আবশ্যক। মাঝে মাঝে ডাক ছেড়ে পাশের পুরুষকে নিজের উপস্থিতি স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ আমার সীমানায় তোমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। তক্ষক দিনের বেলার চেয়ে রাতের বেলায় খাবারের জন্য বেশি সচেতন হয়ে ওঠে। ডিম পাড়ে, কোনোরকমের তা দেয়া ছাড়াই ডিমের খোসা ফেটে বাচ্চা বের হয়ে আসে। আমাদের দেশে ধুসর-সবুজ বা নীলে মিশান দুই ধরনের তক্ষক দেখা যায়।
এই প্রাণীগুলো দিনের পর দিন বনের ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে বনভূমির উন্নয়ন করেছে এবং গ্রামবাংলার ফসলের জমির ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ খেয়ে কৃষকদের ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে অর্থনৈতিক সহায়তা করেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এটি একটি বড় ধরনের ষড়যন্ত্র যা দেশি লোকদের লোভ দেখিয়ে বিদেশিরা এ কাজটি করিয়ে নিচ্ছে। এই প্রাণীগুলো ধ্বংস হলে বন ধ্বংস হবে ফলে বিদেশি কাঠ ও খাদ্যশষ্য আমদানি বাড়বে।
বাংলাদেশে গুইসাপ গোত্রের তিনটি প্রজাতি রয়েছে যাদের দেশের সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। গুই এক ধরনের টিকটিকি। এদের জিহ্বা মসৃণ, খুবই লম্বা, সরু, অগ্রভাগ দ্বিখণ্ডিত, লিকলিক করে এবং সাপের মতো সংকোচনশীল। দানাদার বা গোলাকৃতি আঁশে শরীর আবৃত। গুইসাপ সাধারণত জলাশয়ের কিনারে পুরানো ইঁদুরের গর্তে বা প্রাকৃতিক গর্তে, কিংবা গাছের কোটরিতে বাস করে। শীতের দিনের সকালে এদেরকে অন্যান্য সরীসৃপ প্রাণীদের ন্যায় রোদ পোহাতে দেখা যায়। দিনের বেলায় এরা জলাশয়ের কিনারে বা মানুষের হাঁটা পথের দুইধারে, শাক সবজির জমিতে, হলদি বা শুপারি বাগানে, বাঁশঝাড়ের আশেপাশে, ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে খাদ্যের অম্বেষণ করে। শিকারী কখনো তাড়া করলে পানিতে ডুব দিয়ে অনেক দূরে গিয়ে মাথা উঠিয়ে শিকারীর অবস্থান লক্ষ্য করে। কখনোবা দ্রুত গাছে উঠে পড়ে। প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী গাছে লাফ দিয়ে যেতে দেখা যায়। তাড়া করলে লেজ উঠিয়ে দ্রুত দৌড়াতে থাকে। এদের নির্দিষ্ট বাসভূমি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অন্যস্থানে স্থানান্তর হতে সাধারণত দেখা যায় না।
টিকটিকি গোত্রের প্রাণীরা সম্পূর্ণরূপে মাংসভোজী অথাৎ তারা অন্য ছোট ছোট প্রাণীদের খেয়ে বেঁচে থাকে। টিকটিকিরা সাধারণত লাইটের আলোর মধ্যে আসা মশা, মাছি, মাকড়শা, মথ, বিটল, ফড়িং, ঘাসফড়িং, প্রজাপতি, চেলা, বিছা পোকা, উইপোকা, পিপিলিকা, তোলাপোকাসহ অন্যান্য পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গের ডিম, শুককীট, মুককীট, বা লার্ভা খেয়ে জীবন ধারণ করে ও পরিবেশকে সুন্দর রাখে। রাতের বেলায় দেখা যায় বাড়ির দেয়ালে বা বিদ্যুতের খুঁটিতে টিকটিকিরা বসে থাকে এবং আলোর দিকে উড়ে আসা বিভিন্ন রকমের পোকামাকড় খেয়ে থাকে। ফসলের জমিতে ঘুরে ঘুরে অনিষ্টকারী পোকামাকড় খেতেও তাদেরকে দেখা যায়।
১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের একটি গবেষণা পরিচালনাকালে প্রকৃতি থেকে ২৫টি টিকটিকি ধরে পাকস্থলী উম্মুক্ত করে তাদের খাদ্যাভাস দেখা হয়। বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এরা দৈনিক গড়ে তাদের শরীরের ওজনের শতকরা ৪ দশমিক ৮২ ভাগ পরিমাণ খাবার গ্রহণ করে। পাকস্থলীতে পাওয়া মোট খাদ্য তালিকার (৯৯ শতাংশ) ছিলো প্রাণীজ খাদ্য। প্রাণীজ খাদ্যের মধ্যে শতকরা ৯১ ভাগই ছিলো ফসলের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ এবং শতকরা ৯ ভাগ ছিলো পিপিলিকা, মশা, তেলাপোকা, মাছি, উইপোকা ইত্যাদি। বিটল, ঝিঁঝিঁ পোকা, মাকড়শা, শুঁয়োপোকা, জাতীয় পোকাগুলো প্রায় সব পাকস্থলীতেই পাওয়া গেছে যেগুলো সুপারি, তাল, নারিকেল গাছের কচি মাথা কেটে নষ্ট করে।
১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রাণিবিজ্ঞান জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, প্রকৃতি থেকে ৪৮টি আঞ্জন ধরে তাদের খাদ্যাভাস দেখার জন্য পাকস্থলী বিশ্লেষণ করা হয়। দেখা গেছে এরা দৈনিক গড়ে তাদের শরীরের ওজনের শতকরা ৪ দশমিক ৭৪ ভাগ পরিমাণ খাবার গ্রহণ করে। এদের পাকস্থলীতে মোট ৩৩ প্রজাতির ৩ পর্বের ৩৬৯ ধরনের খাদ্য পাওয়া গেছে তন্মধ্যে ৯৫ দশমিক ৩৯ শতাংশ ছিলো পোকামাকড় এবং ২ দশমিক ৯৮ কেঁচো এবং ১ দশমিক ৬২ শতাংশ ছিলো ছোটছোট শামুক জাতীয় প্রাণী। সবকয়টি পাকস্থলীর মধ্যেই ফসলের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন প্রজাতির কীটপতঙ্গ পাওয়া গেছে। সুতরাং তাদেরকে ফসলের ক্ষতিকারক জীব দমনকারী এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরা প্রাকৃতিকভাবে পেস্ট কন্ট্রোল করে কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।
সাধারণত গুইসাপকে আবর্জনা খাদক বলা হয়। মানুষের ফেলে দেয়া মোরগ-মুরগির নাড়িভুঁড়ি, মাছ বা অন্যান্য প্রাণীর ও উচ্ছিষ্ট অংশ, পড়ে থাকা মৃত মাছ, ব্যাঙ, সাপ, ডিমের খোসা, পাখির ছানা, মুরগীর পালক, বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ, শামুক, ঝিনুক, কাকড়া, কেঁচো, বিছা পোকা, চেলা, ঘাস ফড়িং, মথ, তেলাপোকা ইত্যাদি খাবার গ্রহণ করে পরিবেশকে সুন্দর রাখে তাই তাদেরকে প্রকৃতির ঝাড়ুদার বলা যায়। গবেষণার উদ্দেশে ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ২০টি গুইসাপকে ধরে তাদের শরীরতাত্ত্বিক, শরীরবৃত্তিয় ও খাদ্যাভাস স্টাডি করা হয়। দেখা গেছে এরা দৈনিক গড়ে তাদের শরীরের ওজনের ২% পরিমাণ খাবার গ্রহণ করে। পাকস্থলীতে পাওয়া খাদ্যের মধ্যে শতকরা ৪৩ ভাগই ছিলো কীটপতঙ্গ এবং ৩০.৭৫ ভাগ ছিলো কেঁচো। পাকস্থলীতে পাওয়া বাকি আইটেগুলোর ২৬.২০% ছিলো ইঁদুর, ছোট কচ্ছপের কঙ্কাল, পাখির হাড় ও পালক, শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, ডিমের খোসা, চিংড়ির খোসা, মাছের আঁশ ও কাঁটা, সাপের খোলস, বিভিন্ন ধরনের জলজ পোকা, গোবরে পোকা, চেলা, ঘাস ফড়িং, মথ পোকা, ঝিঁঝিঁ পোকা ইত্যাদি।
দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেকেই জানেন না এসব প্রাণীরা বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোলিং এজেন্ট হিসেবে প্রকৃতিতে কাজ করে এবং কৃষকের বন্ধু হিসেবে কৃষকের অজান্তেই কৃষি পণ্যের ক্ষতিকারক অমেরুদন্ডী ও মেরুদন্ডী পেস্ট কন্ট্রোলিং এজেন্ট বা কৃষি পণ্যের ক্ষতিকারক জীব বা কীটপতঙ্গ দমন করে ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। ফসলের জমির পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বাংলাদেশ সরকার ও প্রাইভেট কোম্পানিগুলো প্রায় ৪০ হাজার টন কীটনাশক (আর্সেনিক, লেড, সালফার, ক্লোরিন, রোটেনন, নিকোটিন, পাইথ্রিন, ডিডিটি, গ্যামাক্সিন, ম্যালাথিয়ন, প্যারাথিন, সেভিন, ডায়াজিনন, ইত্যাদি ঘটিত বিভিন্ন যৌগ) আমদানি করে থাকে।
এই প্রক্রিয়ায় সরকার হারাচ্ছে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা, অন্যদিকে এই সব ওষুধ জমিতে প্রয়োগ করার ফলে ওষুধের পরোক্ষ প্রভাবে মানুষ অসুস্থ্ হচ্ছে, জমির পানি জলাশয়গুলোতে পড়ার কারণে মাছের ডিম ও পোনা মারা যাচ্ছে । ফলশ্রুতিতে মাছের উৎপাদন কমছে, মাছশূন্য হয়ে পড়ছে বহু বিল, হাওর। কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত পোকা মাকড় খেয়ে পাখিসহ প্রকৃতির অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাণিরা মারা যাচ্ছে। বহু প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঐ সব জলাশয়ের পানি ব্যবহারের ফলে মানুষের পেটের পীড়াসহ নানাবিধ রোগ হচ্ছে। অতিমাত্রায় রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন কৃষিজ ও প্রাণিজ খাদ্যের মাধ্যমে কীটনাশক মানবদেহে প্রবেশের কারণে মানুষের হার্ট অ্যাটাক, কিডনি নষ্ট, লিভার সিরোসিস, স্নায়ু এবং ত্বকের বিভিন্ন ধরণের রোগ দেখা দেয়। আরো কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে রাসায়নিক কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করার কারণে প্রস্টেট, যকৃতের ক্যান্সার এবং ফুসফুসসহ বিভিন্ন অঙ্গে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গর্ভবতী মায়েরা ত্রুটিযুক্ত বা অসুস্থ সন্তান জন্ম দেন। প্রায় ত্রিশ হাজার কীটনাশক প্রয়োগকারী কৃষকের স্ত্রীদের নিয়ে একটি সমীক্ষা করে দেখা গেছে তারা বেশির ভাগ আর্নোফসফেটের সংক্রমণের শিকার এবং হরমোনজনিত ক্যান্সার যেমন স্তন, ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার এবং থাইরয়েডের মতো রোগে আক্রান্ত। অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারে অর্থনৈতিক প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রভাব পড়ছে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর।
কীটনাশক ব্যবহার পরিবেশ ও অর্থনীতি উভয়ের ওপরই উল্লেখযোগ্যভাবে খরচ চাপিয়ে দেয়। এই খরচগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক আবাসস্থলের ক্ষতি, ফসলের ফলন হ্রাস এবং স্বাস্থ্যের যত্নের খরচ। ব্যাপক হারে কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে কমে যাচ্ছে জমির উর্বরতা শক্তি এবং মরে যাচ্ছে ফসলের জন্য উপকারী পোকা। সেক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে জীব দিয়ে জীব নিয়ন্ত্রণ চাষাবাদ পদ্ধতি কৃষকদের মাঝে ব্যাপক প্রচলনের পদক্ষেপ নিতে হবে। পৃথিবীর বহুদেশে জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ ব্যবস্থায় ভালো ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে।
বন্যপ্রাণী কীটনাশকের প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল। রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে এই প্রাণীদের স্বাস্থ্য গুরুতর প্রভাবিত হতে পারে। কীটনাশকের ক্ষতি থেকে বন্যপ্রাণীকে রক্ষা করতে, সঠিক পরিমাণ কীটনাশক ব্যবহার করা এবং সঠিক উপায়ে প্রয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ। যে কীটনাশক জমিতে ব্যবহার করা হচ্ছে তা বন্যপ্রাণীর জন্য নিরাপদ কিনা তাও নিশ্চিত করতে হবে। টিকটিকি দেখলেই তাকে মারতে হবে, এ ধরনের মানসিকতা পোষণ করার ফলে দেশের প্রায় সব জেলা থেকেই তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। নির্বিচারে হত্যা, তাদের আবাসভূমি ধ্বংস, বনজ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার, খাদ্যশৃঙ্খল নষ্ট, কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার, বন্যপ্রাণীর রোগ, প্রজনন স্থান ধ্বংস, মানুষের অজ্ঞতা, অহেতুক ভয়, প্রচারে বিমুখতা, মানুষ-টিকটিকি সংঘাত ইত্যাদি কারণে এদের সংখ্যা কমছে। ফলে মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিকভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। আসুন ‘টিকটিকি মারা বন্ধ করি, সুন্দর অর্থনীতি ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলি’।
লেখক: টিম লিডার, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম, পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প ও সাবেক মহাপরিচালক, নায়েম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।