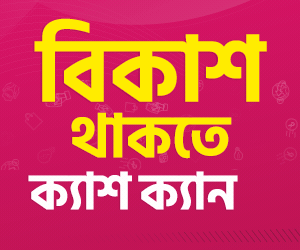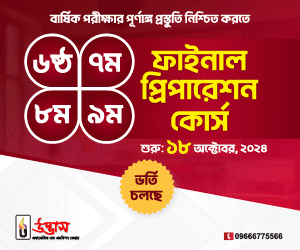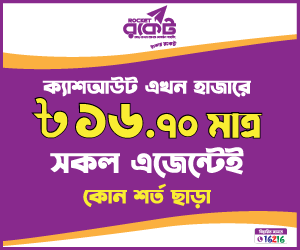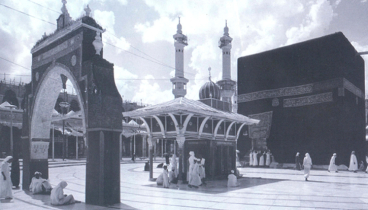বাংলাদেশ আজ একটি সম্ভাবনাময় অর্থনীতির নাম। একসময় যে দেশকে শুধুই উন্নয়ন সহযোগিতার নির্ভরশীল বলে গণ্য করা হতো, সেই বাংলাদেশ এখন বৈশ্বিক বিনিয়োগ মানচিত্রে একটি উদীয়মান গন্তব্য।
গত এক দশকে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা, তরুণ জনগোষ্ঠীর আধিক্য, ভৌগোলিক সুবিধা এবং সরকারপ্রধানের নেতৃত্বে নেয়া প্রগতিশীল অর্থনৈতিক নীতিমালা এই সম্ভাবনার ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে প্রবাহ বাড়ছে, অবকাঠামোগত উন্নয়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি হচ্ছে, এবং নতুন খাতে খোলস ভেঙে এগিয়ে আসছে বাংলাদেশ।
কিন্তু এই সাফল্যের জোয়ারে এক গভীর ফাটল রয়েছে, যা দিন দিন প্রকট হচ্ছে। তা হলো-দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের সংকট। বিনিয়োগ যেমন পুঁজি, অবকাঠামো ও নীতিনির্ধারণের ওপর নির্ভর করে, তেমনি দক্ষ জনশক্তির ওপরও তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়। এখানেই বাংলাদেশের বড় দুর্বলতা লুকিয়ে আছে।
এই প্রবন্ধে আমরা বিনিয়োগ সম্ভাবনার বাস্তব চিত্র, দক্ষতার অভাবের প্রকৃতি ও প্রভাব, এবং এই সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য গৃহীত ও সম্ভাব্য উদ্যোগ নিয়ে বিশদ আলোচনা করবো।
বাংলাদেশে বিনিয়োগের গতি গত কয়েক বছরে নজরকাড়া। অভ্যন্তরীণভাবে তৈরি পোশাক, কৃষিভিত্তিক শিল্প, নির্মাণ, ওষুধ এবং পরিষেবা খাতে দেশীয় উদ্যোক্তারা নতুন নতুন প্রকল্পে ঝুঁকছেন।
তরুণদের সাহসী পদক্ষেপে আইটি, ই-কমার্স ও ফিনটেকেও নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। সরকারি পর্যায়ে পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কিংবা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো প্রকল্প শুধুই উন্নয়নমূলক নয়, বরং বিনিয়োগের পরিকাঠামো শক্তিশালী করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
অন্যদিকে, বিদেশি বিনিয়োগও বাড়ছে। বিশ্বব্যাংক ও ইউএনসিটিএডি-এর তথ্য অনুযায়ী, গত এক দশকে বাংলাদেশে বার্ষিক গড় এপডিআই ছিলো প্রায় ২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার।
২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে এই অঙ্ক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৫ বিলিয়নে, যা ইতিবাচক প্রবণতার ইঙ্গিত। চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে।
বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন, হাইটেক পার্ক ও স্টার্টআপ ইনকিউবেটরের মতো উদ্যোগগুলো বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গঠনে সহায়ক হচ্ছে, যদিও বাস্তবায়ন ও নীতিগত স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে এখনো অনেক কিছু করার বাকি।
বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান তাকে দক্ষিণ এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেয়। ভারতের বিশাল বাজার, চীনের উৎপাদন কেন্দ্র, এবং আসিয়ান অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বলয়-এই সবের মাঝখানে অবস্থান বাংলাদেশের।
ট্রানজিট সুবিধা, সমুদ্রবন্দর, রেল ও সড়ক নেটওয়ার্কের বিকাশ একে একটি লজিস্টিক হাবে পরিণত করার সুযোগ তৈরি করছে।
তারও চেয়েও বড় সম্পদ বাংলাদেশের তরুণ জনসংখ্যা। ৬৫ শতাংশ মানুষ কর্মক্ষম বয়সে, যা একটি ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড’ হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু এই সম্পদকে কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট দক্ষতা-যা বর্তমানে ঘাটতির মুখে।
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ৮৫ শতাংশ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পায়নি। অনেকেই অপ্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা বা হাতে-কলমে শেখার ওপর নির্ভর করে পেশাজীবনে প্রবেশ করেন। এর ফলে আধুনিক শিল্পখাতে যেমন প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বা ইলেকট্রনিক্স অ্যাসেম্বলি-এইসব ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মী পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।
মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা এখনো পরীক্ষানির্ভর এবং প্রথাগত পদ্ধতিতে চলে। বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ, এসটিইএম শিক্ষা বা কোডিং, রোবোটিক্সের মতো বিষয়গুলো এখনো শহরকেন্দ্রিক এবং সীমিত পরিসরে সীমাবদ্ধ। উচ্চশিক্ষা শেষ করা অনেক শিক্ষার্থীই বাস্তব চাকরি বা উদ্যোক্তাপ্রসূত চাহিদার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন না।
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যায় কিছুটা অগ্রগতি হলেও মানের দিক থেকে এখনো অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে। সরকারি-বেসরকারি টিটিসি, টিএসসিগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি, দক্ষ প্রশিক্ষক, এবং শিল্পখাতের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগের অভাব প্রকট।
এই দক্ষতার সংকট সরাসরি বিনিয়োগকারীদের আস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বহু আন্তর্জাতিক কোম্পানি বাংলাদেশে আগ্রহী হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয়ভাবে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান বা অপারেটর না পাওয়ায় তারা ধীর পদক্ষেপ নেয় বা অন্য গন্তব্যে বিনিয়োগ সরিয়ে নেয়।
বিশ্বব্যাপী আউটসোর্সিং খাতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এখনো সীমিত। প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার আইটি গ্র্যাজুয়েট তৈরি হলেও, তাদের মধ্যে মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশই আন্তর্জাতিক মানের। ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান অনেক নিচে, যেখানে এককভাবে ভারতই গ্লোবাল আউটসোর্সিংয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছে।
চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে অটোমেশন, মেশিন লার্নিং, রোবটিক্স বা আইওটির মতো প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই শিল্পক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এই প্রযুক্তির প্রয়োগে দক্ষ মানবসম্পদের অভাব শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিযোগিতার বাইরে ছিটকে ফেলছে। বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় বেশ কিছু কাঠামোগত দুর্বলতা রয়ে গেছে।
প্রথমত, এখনো দেশে একটি কেন্দ্রীয় স্কিল ডেটাবেইজ নেই। কোন খাতে কী পরিমাণ দক্ষ জনবল দরকার এবং বর্তমানে কতোটুকু আছে--সেই তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা অনুপস্থিত। ফলে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় এলোমেলোতা দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং বা দক্ষতা বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম কার্যকর নয়। অনেক শিক্ষার্থী জানেই না কোন খাতে কাজের চাহিদা রয়েছে কিংবা কীভাবে সে দক্ষতা অর্জন করবে।
তৃতীয়ত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্প খাতের মধ্যে সংযোগ দুর্বল। ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করা হয় না, ফলে তৈরি হয় এক ‘স্কিল গ্যাপ’। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন বহুমাত্রিক উদ্যোগ। প্রথমত, শিক্ষাব্যবস্থায় দক্ষতা ভিত্তিক পরিবর্তন আনতে হবে। পাঠ্যক্রমে সমস্যা নির্ভর শেখার পদ্ধতি, কোডিং বা রোবোটিক্সের মতো বিষয়ে জোর দিতে হবে। স্কুল থেকেই প্রযুক্তিনির্ভর চিন্তা-ভাবনার বীজ বপন করতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিল্পখাতের সঙ্গে যৌথ গবেষণা, ইন্টার্নশিপ এবং প্রকল্প-ভিত্তিক শেখার সুযোগ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিকায়ন করা জরুরি। সরকারি-বেসরকারি টিটিসিতে নতুন যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বে তৈরি মডিউল প্রয়োজন। প্রতিটি অঞ্চলের চাহিদা বুঝে অঞ্চলভিত্তিক দক্ষতা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।
তৃতীয়ত, একটি জাতীয় স্কিল ব্যাংক গড়ে তুলে দেশে কোন খাতে কতো দক্ষতা দরকার তার ম্যাপিং করতে হবে। অনলাইনভিত্তিক সার্টিফিকেশন কোর্স চালু করতে হবে যাতে প্রত্যন্ত এলাকার যুবকরাও যুক্ত হতে পারে।
চতুর্থত, বেসরকারি খাতকে এই উদ্যোগে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। কর রেয়াত বা ভর্তুকির মাধ্যমে স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি, ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রমে উৎসাহ দেয়া যেতে পারে।
সবশেষে, একটি সামগ্রিক নীতি প্রয়োজন। যেমন ‘স্কিলস ফর ইনভেস্টমেন্ট’ নামের একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত নীতি গ্রহণ করে শিক্ষা, শিল্প ও আইসিটি বিভাগের সমন্বয়ে একটি বাস্তবভিত্তিক রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক স্কিল সার্টিফিকেশনের সঙ্গে দেশীয় সনদের সমতা আনার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।
বাংলাদেশ এখন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে প্রবল সম্ভাবনা, অন্যদিকে প্রস্তুতির অভাব। এই গ্লোবাল প্রতিযোগিতার যুগে কেবল অবকাঠামো দিয়ে টিকে থাকা যাবে না—টিকে থাকতে হবে দক্ষতায়, উদ্ভাবনে এবং প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারে।
সঠিক দক্ষতার অনুপস্থিতিতে বিনিয়োগ এসে থমকে যেতে পারে, বা শ্রমবাজারে বেকারত্বের নতুন চাপ তৈরি হতে পারে।
তাই এই মুহূর্তে প্রয়োজন একটি ‘স্কিল রেভল্যুশন’, যা শুধু সরকারি উদ্যোগ নয়, বরং সামাজিক সচেতনতা, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণে সম্ভব। বিনিয়োগ তখনই আসে, যখন বিশ্বাস থাকে-আর বিশ্বাস তখনই আসে, যখন দক্ষতা থাকে।
লেখক: প্রোগ্রাম ম্যানেজার, পিকেএসএফ