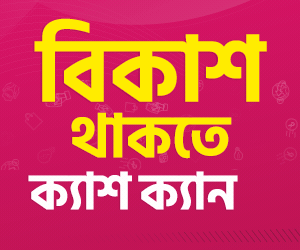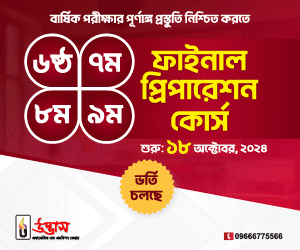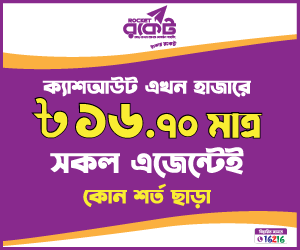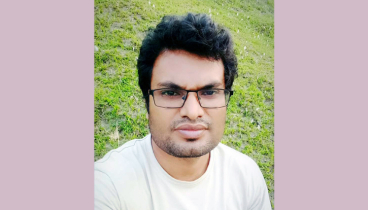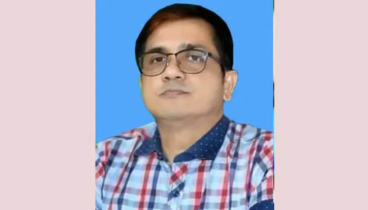বাংলাদেশের শিক্ষা এক বিশাল পরিবার। এর সদস্য সংখ্যা এতো বিশাল যে, শুধু ডালভাত খাইয়ে এই সদস্যদের লালন-পালন করতেই বড় অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন। পুরাতন ভবন মেরামত, নতুন ভবন তৈরি, শিক্ষা উপকরণ ও বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি বিষয়গুলো সীমিত পরিমাণ শিক্ষা বাজেটে কোনোভাবে কুলায় না।
যেনতেন প্রকারে সেগুলো করা হয়। হয়তো দ্রুত ১০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন মেরামত করতে হবে, ফার্ণিচার প্রয়োজন বিশ হাজার প্রতিষ্ঠানে সেখানে হয়তো হাজার তিনেকের অর্থ ছাড় হয় বহু ধস্তাধস্তি করে। এগুলোর সঙ্গে শিক্ষার মানের সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও এগুলো শিক্ষায় মারাত্মক ভূমিকা পালন করে।
শিক্ষার মানের সঙ্গে অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের শ্রেণি উপযোগী যেসব বিষয় জানার ও আয়ত্ত করার কথা শিক্ষার্থীরা সেগুলো থেকে বহুদূরে অবস্থান করেন। কিন্তু সবই চলে অর্থাৎ ক্লাস, পরীক্ষা, পাবলিক পরীক্ষা এগুলো সবই প্রচলিত নিয়মে চলে। শিক্ষার্থীদের যা জানার কথা, পারার কথা, যা যা অর্জন করার কথা সেগুলো অর্জিত হচ্ছে না।
যেমন-এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, উত্তরপত্র মূল্যায়ন হয়, শিক্ষার্থীরা শতভাগ পাশের কাছাকাছি অবস্থান করে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা এসএসসি লেভেলের থাকে না আাশি শতাংশের মতো শিক্ষার্থীদের। বিষয়টি প্রমাণ করারও তেমন কোনো ব্যবস্থাও নেই। তবে, ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় কিছুটা হলেও শিক্ষার্থীদের মানের অবস্থানটি বোঝা যায়।
মেডিক্যালে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হন, প্রকৃত মেধাবীদের না পাওয়ায় দুর্বল শিক্ষার্থীদের দিয়ে সিট পূরণ করা হচ্ছে। সেটি মাত্র কদিন আগে পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয়েছে। এ বিষয়গুলো কি জিডিপির ৬ শতাংশ বা বাজেটের ২০ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করলেই সবই ঠিক হয়ে যাবে?
চাপা পড়ে থাকা এবং চেপে রাখা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর যে অজস্র সমস্যা সেগুলো আগ্নেয়গিরির মতো বের হতে শুরু করেছে আর তার দাহে পুড়ছে পুরো দেশ, চরম উত্তাপে ভুগছে জনগণ। শিক্ষার্থীরা সব রাস্তায়, সবাই জনগণের রাস্তা বন্ধ করে অন্তর্বর্তী সরকারের ঘাড়ে চাপ দিয়ে যুগ যুগ ধরে জিইয়ে রাখা সমস্যা সমাধানের জন্য চরম পথ বেছে নিচ্ছেন, অচল করে দিচ্ছেন সব।
এই অবস্থায় শিক্ষার কোন বাজেট এসব সমস্যা দূর করবে? ধরুন, এক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের আবাসন সমস্যার সমাধান চাচ্ছেন। বন্ধ করে দিলেন ঢাকা সিটির অর্ধেক। তাদের আবাসন সমস্যাই যদি রাষ্ট্রের শিক্ষা বাজেট দিয়ে সমাধান করার কথা চিন্তা করা হয় তাহলে দেখা যাবে কাটছাঁট করতে হবে অনেক কিছু।
শুধু জগন্নাথ নয়, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ২১টিতে ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধার বাইরে। বেসরকারিগুলোতে তো আবাসন সুবধিাই নেই। দরিদ্র অর্থনীতিতে শিক্ষার যে বাজেট তাতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনও ঠিক মতো দেয়া যায় না। এর মধ্যে আবার সবাই চাচ্ছেন জাতীয়করণ, তার মানে আরো কয়েক হাজার কোটি টাকা।
তারপর জরুরি কোনো অবস্থা মোকাবিলা করা আর শিক্ষার জন্য নতুন কিছু করা, প্রতিষ্ঠান সংষ্কার ও মেরামত করা এসব তো করার বাজেট কোথায়? তাহলে এই ৬ শতাংশ জিডিপি কিংবা ২০ শতাংশ জাতীয় বাজেট শিক্ষায় ব্যয় করার কথা কী এই অবস্থায় কতোটা কার্যকরী? এর ওপর আবার চারদিকে শত্রুর হানাহানি। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই প্রতিরক্ষা ব্যয় থাকে সবচেয়ে বেশি, দেশের এখন যে পরিস্থিতি তাতে প্রতিরক্ষা ব্যয় আরো বাড়ানো হচ্ছে। জাতীয় আয়ের মোটা অংশ সেখানে গেলে শিক্ষার কতোটা কী থাকবে বলা মুশকিল।
শিক্ষার জন্য ব্যয় যেভাবে এবং যে ধারায় চলছে সেটি কোনো স্বাভাবিক বিষয় নয়। এজন্য প্রয়োজন মহাপরিকল্পনা, মহাপ্ল্যান ও মহা নতুন উদ্ভাবন। কারণ, সম্পদ সীমিত, অবস্থা বেগতিক, অর্থের টানাটানি আর সবার দাবি-দাওয়া অসীম। কীভাবে কী হবে? এখানে শুধু গৎবাঁধা সেই বাজেটের এতো শতাংশ শিক্ষায় ব্যয় করলেই সব সমাধান হয়ে যাবে বলে অনেকে মনে করেন।
বিষয়টি তা নয়। দেশ এখন প্রত্যক্ষ করছে রাষ্ট্র পরিচালিত যতো বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ আছে সবগুলোই যেনো জনদুর্ভোগের কারখানায় পরিণত হয়েছে। কোনো বেসরকারি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু জনদুর্ভোগ সেভাবে বাড়াচ্ছে না, বাড়াচ্ছে শুধু রাষ্ট্রয়াত্তগুলো। এখানে সমস্যার যেনো শেষ নেই। এসব ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা, কোন পদ্ধতি, কোন স্ট্র্যাটেজি যে কাজ করবে বুঝে ওঠা কঠিন। কাজেই এবারের বাজেট এতোবড় বড় অগ্নুৎপাতে কীভাবে পানি ঢেলে কিংবা কোন উপায়ে স্বাভাবিক আনা যাবে তার কোনো প্রেসক্রিপশন দেখতে পাচ্ছি না।
শিক্ষাখাতে বাজেটের সীমাবদ্ধতা আমাদের অগ্রগতির অন্যতম বড় বাধা বলে আমরা মনে করি, যেটিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এর সঙ্গে আরো কথা আছে যেগুলো নিয়ে সেভাবে আলোচনা হয় না। তাই বাজেটে কেবল বরাদ্দ বাড়লেই হবে না, বরং বাজেটের অভ্যন্তরীণ কাঠামো পুনর্গঠন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণেই আমাদের মূল মনেযোগ দিতে হবে।
রাজস্ব আহরণে ধীরগতি, কর ও শুল্কে নিম্ন প্রবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক ঋণের কিস্তি পরিশোধের চাপের কারণে বার্ষিক বাজেটের আকার না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। অনেক ফুটপাতের দোকানদার যারা মোটিভেটেড তারা ধীরে ধীরে ব্যবসার আদ্যোপান্ত শিখে, সমস্ত কৌশল শিখে ছোট একটি স্থায়ী দোকান দেন, তারপর বড় দোকান দেন এবং সফল ব্যবসায়ী হোন।
তারা কিন্তু হঠাৎ বিশাল এক অঙ্কের নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন না। অপরদিকে, কিছু কিছু লোকজনদের দেখা যায়, জীবনে ব্যবসা করেননি হঠাৎ করে ব্যাংকের লোন নিয়ে, কিংবা ধনী আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিরাট এক ব্যবসা শুরু করেন, বিশাল বিশাল শো-রুম কিংবা এই জাতীয় টেকনিক অবলম্বন করেন কয়েকমাস কিংবা বছর পরে দেখা যায় ব্যবসায় লালাবাতি জ্বালিয়ে সবকিছু হারিয়ে পথে বসেন।
কারণ, ব্যবসা না শিখে হঠাৎ বিশাল বাজেট পেয়ে যা শুরু করেছিলেন সেখানে তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। অনেকেই বলে থাকেন অর্থ হলেই আমাদের শিক্ষার সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, ব্যাপারটি সে রকম নয়। আমার প্রাথমিক শিক্ষা সরকারি, শিক্ষকরা রাষ্ট্রের সব সুবিধা পাচ্ছেন কিন্তু সেখানে শিক্ষা নেই। দেশের অনেক অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা।
দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিশাল বিশাল ভবন, নয়ন জোড়ানো ক্যাম্পাস, কোটি কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় বাজেট কিন্তু যুগোপযোগী শিক্ষা সেখানে নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মানে গবেষণা, এখানে কোনো গবেষণা হয় না। কারণ, বাজেট নেই। গবেষণা মানে তো এই নয় যে, কিছু অর্থ পাওয়া গেলো, তা দিয়ে কিছু ডাটা সংঘ্রহ করলাম এবং সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ করে কিছু রেকমেন্ডেশন দিলাম। এটি আগ্রহের বিষয়, এটি প্রকৃতভাবে বাস্তবধর্মী কাজ সেটি সেভাবে কেউ করার তাগিদ অনুভব করছেন না বলে সেভাবে গবেষণা হচ্ছে না। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও গবেষণা সেভাবে হচ্ছে না তবে রাষ্ট্র কোনো অর্থ খরচ করে না। অথচ অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই যুগের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থী তৈরি হচ্ছে।
কিছু অর্থনীতিবিদগন তাই বলেছেন, শুধু টাকার বরাদ্দ বাড়িয়ে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি সম্ভব নয়। তাই বাজেটে কেবল বরাদ্দ বাড়লে হবে না, বরং বাজেটের অভ্যন্তরীণ কাঠামো পুনর্গঠন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণেই আমাদের মূল মনেযোগ দিতে হবে।
রাজস্ব আহরণে ধীরগতি, কর ও শুল্কে নিম্ন প্রবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক ঋণের কিস্তি পরিশোধের চাপের কারণে বার্ষিক বাজেটের আকার না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রাথমিকভাবে আসন্ন বাজেটের আকার নতুন বাজেটের আকার ৭ লাখ ৫৯ হাজার ৯৫৫ কোটি টাকা হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে।
বৈশ্বিক নানা টানাপোড়েনের এ সময়ে আগামী বাজেটের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করা হচ্ছে সুদের টাকা পরিশোধ, জনকল্যাণে বড় আকারের ভর্তুকি দেয়া ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের শর্ত মেনে রাজস্ব আদায়ের অঙ্ক বাড়ানো। এগুলো যৌক্তিক চিন্তা বলে মনে হচ্ছে।
সরকারি বেসরকারি বলে কথা নেই, শিক্ষা কীভাবে কার্যকরী হতে পারে যেখানে মেধাবীরা শিক্ষকতায় আসবেন, শিক্ষকতায় এসে তারা যাতে অর্থ কষ্টে না ভোগেন, সামাজিক মর্যাদা হানি না হয় সে ধরনের এক ইনোভেটিভ পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। সেটি কোনো দেশের উদাহরণ টেনে হবে না। কারণ, আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট, অর্থনীতি ও কালচার অন্যান্য দেশের সঙ্গে মিলবে না। আমাদের মতোই ব্যবস্থা করতে হবে সেটি কীভাবে? কে করবেন সেটি?
শিক্ষায় পরিবর্তনটা আসলে আনবেন কে? মন্ত্রণালয় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু মন্ত্রণালয় যারা চালান তারা প্রায় সবাই প্রশাসন ক্যাডারের এবং তাদের চাকির বদলিযোগ্য। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো গতমাসে ছিলেন পাট মন্ত্রণালয়ে, কেউ ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ে, কেউবা অবার ছিলেন বস্ত্র মন্ত্রণায়ে—এ মাসে এসে হঠাৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা। এ মন্ত্রণালয়েও কমাস বা কবছর থাকবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।
তারা শিক্ষার যে গুরুত্বর অসুস্থতা, যে ক্রোনিক ডিজিজ সেসব ক্ষেত্রে তো তাদের কোন ধারণা নেই, থাকার কথাও নয় এবং বলতে গেলে প্রয়োজনও নেই। কারণ, আগামী কোনো মাসে আবার তাকে কোনো মন্ত্রণালয়ে পোস্টিং দেয়া হবে তার কোনো ঠিক নেই।
জনপ্রতিনিধি হিসেবে যেসব মন্ত্রীরা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পদে থাকেন তাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে রাজনীতি। তারা রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, শিক্ষায় পুরোপুরি রাজনীতির বিষয়গুলোর কোনটিতে তারা লাভবান হবেন ইত্যাদি নিয়ে তাদের চিন্তা থাকে যেগুলো আমরা বহুদিন এবং বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করেছি।
শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন নিয়ে তাদের তেমন কোনো পদক্ষেপ আমরা দেখিনি। কর্মীরা, পার্টি কোনটিতে বেশি লাভবান হবেন তাদের চিন্তা থাকে সেসব নিয়ে। আর শিক্ষা নিয়ে তাদের এতো গভীরে ধারণাও থাকে না যে, বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন তারা নিয়ে আসবেন।
বিশেষ সরকারের সময়ে যারা উপদেষ্টা বা এই ধরনের দায়িত্বে থাকেন তারা নিখাদ ভদ্রলোক। শিক্ষার জটিল প্যাঁচ, বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে ডিল করা তাদের জন্য বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষায় যেসব দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট গড়ে ওঠে সেগুলোর সঙ্গে পেরে ওঠেন না, পারার কথাও না। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদ ও গবেষক যারা শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা রাখেন তাদের কিছু একটা করতে পারার কথা কিন্তু তাদের দেখা যায় শুধু উপদেশ দিতে, রেকমেন্ডেশন তৈরি করতে, যার অধিকাংশরই বাস্তবের সঙ্গে মিল থাকে না।
শিক্ষার দীর্ঘদিনের এবং বাস্তবধর্মী সমাধান দিতে পারার কথা শিক্ষক সংগঠনগুলোর, তুখোর শিক্ষক নেতাদের। তারা বাস্তবমুখী কিছু প্রেসক্রিপশন দিলে সেগুলো অনেকটাই কাজে লাগার কথা। কিন্তু তারা এসব একাডেমিক বা শিক্ষার ধারে কাছেও নেই। তারা শুধুমাত্র অর্থিক সুবিধাদি নিয়ে আলোচনায বেশি ব্যস্ত ফলে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বা মূল্য কারোর কাছেই নেই। কাজেই শিক্ষার দুর্দশা কাটানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এটি হঠাৎ বাজেট বাড়ানোর বিষয় নয়।
বাজেট যদিও বাড়ানো হবে, কোথায় সেটি ব্যয় হবে তার সঠিক নির্দেশনা, ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে পরিকল্পনা থাকা দরকার, সেটি কে করবেন? শিক্ষার উন্নয়নের কথা আসলেই সবাই শিক্ষক প্রশিক্ষণের কথা বলেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণের নামে শিক্ষকদের তথ্যে ভরপুর করে রাখা হয়, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয় কিন্তু শিক্ষার কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? শ্রেণিকক্ষে কি তার কোনো প্রতিফলন আছে বা থাকলে কোন মেকানিজমে আছে? শিক্ষার মান বরং নিচের দিকেই। এখানেও কী পরিবর্তন দরকার সেটিও বিরাট পরিকল্পনার ব্যাপার, ইনোভেশনের ব্যাপার। কে করবেন সেসব?
লেখক: ক্যাডেট কলেজের সাবেক শিক্ষক