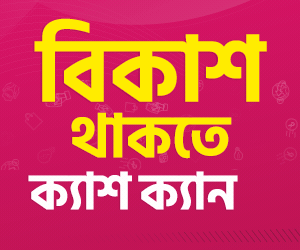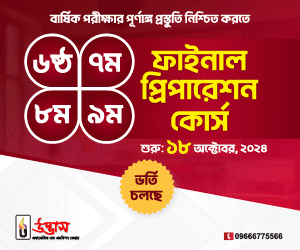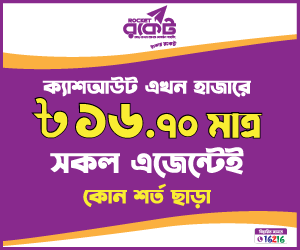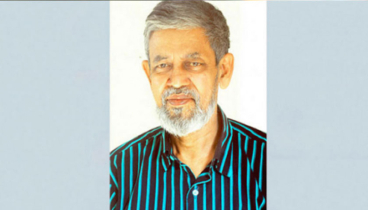প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী ৩ মে পালিত হয় ‘বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস’। এটি শুধু একটি স্মরণ দিবস নয়, বরং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ে আত্মনিবেদিত সাংবাদিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে সাংবাদিকতার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়ার দিন। বাংলাদেশে এ দিবস পালিত হয় এক ধরনের দ্বৈত বাস্তবতায়- একদিকে রঙিন ব্যানারে স্বাধীনতার উৎসব, অন্যদিকে সাংবাদিকদের মুখে তীব্র হতাশা আর ক্ষোভের ঝাঁঝ।
এই কলামে আমরা আলোচনা করবো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মুক্ত গণমাধ্যমের বর্তমান অবস্থা, আইনি ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ, রাষ্ট্রের ভূমিকা, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, ডিজিটাল যুগের নতুন প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা।
একটি প্রশ্নের মুখোমুখি বাংলাদেশ
‘বাংলাদেশে কি সত্যিকারের মুক্ত গণমাধ্যম আছে?’ এই প্রশ্ন আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্রে, এমনকি চায়ের দোকানের আলোচনাতেও উচ্চারিত হয়। সংবিধানে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হলেও বাস্তবতায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অনেকটাই সীমাবদ্ধ। বলে মনে করেন সাংবাদিক ও বিশ্লেষকরা।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমাগত পিছিয়ে গেছে। ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের ‘Reporters Without Borders’-এর প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে বাংলাদেশ অবস্থান তলানিতে। যেখানে প্রতিবেশী নেপাল, ভুটান, এমনকি ভারতও বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে রয়েছে। এই পতনের পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, ভয়ভীতি, এবং আইনের অপব্যবহার। বলেও ধারণা করা হয়ে থাকে।
আইনি শৃঙ্খলে সংবাদমাধ্যমঃ
বাংলাদেশে সংবাদপত্র ও অনলাইন মিডিয়ার ওপর সরাসরি কিংবা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার হলো আইন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ), অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, কিংবা সম্প্রতি আলোচিত সাইবার নিরাপত্তা আইন- এই সব আইনের মূল উদ্দেশ্য যদি হয় সাইবার অপরাধ রোধ, বাস্তবে সেগুলো হয়ে উঠেছে ভিন্নমত দমন ও সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধের উপায়। ঠিক এইসব আইনেই সাংবাদিকদের দমন করা যায় খুব সহজে। যা মুক্ত সাংবাদিকতার জন্য প্রতিবন্ধকতা।
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ২০১৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সাংবাদিক ও লেখকদের বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা হয়েছে, যাদের মধ্যে অনেকেই শুধুমাত্র মতামত প্রকাশের দায়ে গ্রেপ্তার কিংবা হয়রানির শিকার হয়েছেন। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আইনি ও নৈতিক উভয় দিক থেকেই আক্রান্ত হয়েছে। এর ফলে সাংবাদিকরা আরো নিয়ন্ত্রিত আচরণের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন বলেও অভিমত সংশ্লিষ্ট সকলের।
রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও বাজার দখলের কৌশলঃ
বাংলাদেশের গণমাধ্যমের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো রাষ্ট্রের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসায়িক দখলনীতি। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর মালিকানায় সরকারঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আধিপত্য এবং বিজ্ঞাপন বণ্টনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ, স্বাধীন সাংবাদিকতার অন্যতম বাধা।
সরকারি বিজ্ঞাপন বরাদ্দ কিংবা প্রত্যাহারের হুমকি, কর জটিলতা, কিংবা হঠাৎ করে সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার নজির সংবাদমাধ্যমগুলোকে আত্মনিয়ন্ত্রণ বা ‘সেলফ সেন্সরশিপ’-এ বাধ্য করছে। এমনকি কিছু নামি-দামি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক সুবিধার্থে স্বেচ্ছায় তাদের নৈতিক অবস্থান বিসর্জন দিয়েছে।
২৪ এর অভ্যুত্থান পরবর্তী সময় টিভি আর সাম্প্রতিক দীপ্ত টিভিসহ আরো ২ টি টিভির সংবাদকর্মীদের চাকুরিচ্যুতি সে বার্তাকে আরো স্পষ্ট করেছে।
সাংবাদিকদের নিরাপত্তাহীনতা ও পেশাগত ঝুঁকিঃ
বাংলাদেশে সাংবাদিকতা একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। ২০২০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ৩০০-এর বেশি সাংবাদিক হামলা, মামলা বা হুমকির শিকার হয়েছেন। বিভিন্ন সূত্র মতে। অনেকে মারধরের শিকার হয়েছেন মাঠে রিপোর্ট করতে গিয়ে। অথচ অপরাধীদের বিচার হয়েছে এমন উদাহরণ নেই বললেই চলে।
মফস্বলে কর্মরত সাংবাদিকরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিংবা প্রভাবশালী মহলের রোষানলে পড়েন তারা। সাংবাদিক ইউনিয়ন ও প্রেস ক্লাবগুলো অনেক সময় তাদের পাশে দাঁড়ালেও, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বা সুরক্ষা নিশ্চিত করার উদ্যোগ তেমন চোখে পড়ে না। যার কারণে সংবাদমাধ্যমে সম্পৃক্ত সকলেই নিজেকে আরো অসহায় অবস্থায় দেখতে পান। যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।
নতুন প্রজন্ম ও ডিজিটাল সাংবাদিকতার সম্ভাবনাঃ
তবে অন্ধকারের মাঝেও আশার আলো আছে। ডিজিটাল সাংবাদিকতা নতুন এক মুক্তির দিগন্ত খুলে দিয়েছে। অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ইউটিউব ভিত্তিক নিউজ চ্যানেল, পডকাস্ট- এইসব মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম যুক্ত হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নাগরিক সাংবাদিকতার উত্থান সংবাদ প্রকাশে নতুন পথ দেখাচ্ছে।
তবে এখানেও আছে সীমাবদ্ধতা। ভুয়া খবর, ‘ফেক নিউজ’, বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে পড়া এবং তথ্য যাচাই না করার প্রবণতা গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে। তাছাড়া ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মও এখন নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের আওতায় চলে আসছে।
নারী সাংবাদিকদের দ্বিগুণ সংগ্রামঃ
বাংলাদেশে নারী সাংবাদিকদের সংখ্যা বাড়লেও তাদের পেশাগত চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। কর্মক্ষেত্রে হয়রানি, নিরাপত্তাহীনতা, এবং নেতৃত্বে অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা তাদের পথকে আরো কঠিন করে তোলে। অনেক সময় সংবাদের গঠনমূলক দিকগুলোতে নারী সাংবাদিকদের অবদান অস্বীকার করা হয়।
একটি মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণমাধ্যম কেবল তখনই সম্ভব, যখন সকল লিঙ্গের সাংবাদিকরা সমানভাবে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে পারবেন। যা কেবলই সকলের প্রতিশ্রুতিতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।
রাষ্ট্র কি গণমাধ্যমের বন্ধু হতে পারবে?
একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার ও গণমাধ্যমের সম্পর্ক হওয়া উচিত পারস্পরিক নির্ভরতার, অবিশ্বাসের নয়। সাংবাদিকরা রাষ্ট্রের শত্রু নয়- তারা রাষ্ট্রকে সঠিক পথে রাখার অভ্যন্তরীণ প্রহরী। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশে বহু সময়েই সরকার সাংবাদিকতাকে ‘বিরোধিতা’ বা ‘ষড়যন্ত্র’ হিসেবে দেখেছে।
রাষ্ট্র যদি চায় একটি উন্নয়নমূলক, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ, তাহলে প্রথমেই তাকে মুক্ত ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের পক্ষে অবস্থান নিতে হবে।
মুক্তির পথ কোথায়?
মুক্ত গণমাধ্যম কোনো অলংকার নয়- এটি একটি জাতির বিবেক। স্বাধীন সাংবাদিকতা ছাড়া গণতন্ত্র যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি উন্নয়নও হয়ে ওঠে একপাক্ষিক। বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় মুক্ত গণমাধ্যম দিবস পালন যেনো এক ধরনের আত্মজিজ্ঞাসা। আমরা কি সত্যিই মুক্ত? এই প্রশ্ন এসে যায়। বারবার সামনে আসে। তবে উত্তর মেলে না।
এই দিনে আমাদের উচিত শুধুমাত্র শোক বা শ্লোগান নয়, বরং আত্মসমালোচনা ও প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে নতুন করে ভাবা- কীভাবে আমরা একটি সত্যনিষ্ঠ, সাহসী ও মানবিক গণমাধ্যম গড়ে তুলতে পারি। যেখানে সাংবাদিকতা হবে ভয়হীন, তথ্যভিত্তিক এবং জনগণের পক্ষে, মানবতার পক্ষে বক্তব্য আরও স্পষ্ট হবে।
পরিশেষে, একটি স্বাধীন সংবাদমাধ্যম কেবল সাংবাদিকদের বিষয় নয়- এটি আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের অধিকারের সঙ্গে জড়িত। কারণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানে মানুষের জানার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পরিবেশ। মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে তাই রাষ্ট্র, সমাজ, এবং সাংবাদিকদের সবাইকে নিয়ে নতুন এক জাগরণ ঘটুক- স্বাধীনতার নয়, দায়িত্বের।
লেখক: অ্যাডভোকেট