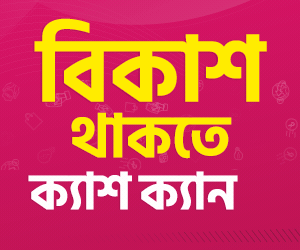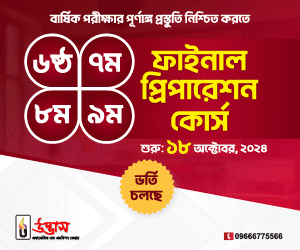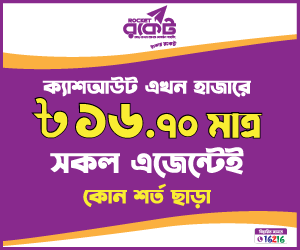বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সারা জীবন সাহিত্যচর্চায় শুধু বাংলা সাহিত্যভান্ডারকে সমৃদ্ধই করেননি, একই সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাংলা সাহিত্যকে পৌঁছে দিয়েছেন। এমনকি বিশ্বের বিখ্যাত সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সরাসরি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের।
তার জন্মস্থান ভারতের বাইরে ইংল্যান্ডের পর আমেরিকাতেই তিনি সবচেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করেছেন। ১৯১২ থেকে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঁচবার আমেরিকা ভ্রমণ করেন। তিনি মোট ১৭ মাস আমেরিকায় অবস্থান করেছিলেন। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর সারা বিশ্ব রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে।
ফলে বিভিন্ন দেশ থেকে আসতে থাকে আমন্ত্রণ। সেসব আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে জাহাজে বহু দেশে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ৫ মহাদেশের ৩৩টির বেশি দেশ ভ্রমণ করেন। তবে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা বাদ দিলে অন্য দেশগুলো ভ্রমণ করেছেন ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির পরপর।
দেশগুলো হলো ফ্রান্স, হংকং, চীন, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, আর্জেন্টিনা, ইতালি, নরওয়ে, হাঙ্গেরি, যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, গ্রিস, মিসর, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, জাপান, মিয়ানমার, হল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইরান, ইরাক ও শ্রীলঙ্কা। আমেরিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিলো বিশেষ সম্পর্ক। আমেরিকা ও আমেরিকানদের প্রতি তাঁর একধরনের আসক্তি জন্মেছিল, যা তাঁকে বারবার আমেরিকায় নিয়ে এসেছে।
আমেরিকার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণের আরেকটি উদাহরণ হলো তাঁর একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষিবিষয়ক উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় প্রেরণ। সেই সময় সাধারণত সচ্ছল ভারতীয় অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য নির্বাচন করতেন বিলেত, এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যতিক্রম। আমেরিকা আসার পেছনে আরো কিছু ঘটনা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো।
বাল্যকালে পড়া আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের আত্মজীবনী তাঁকে আমেরিকার প্রতি উৎসুক করে তুলেছিলো। এ ছাড়া আমেরিকার সাহিত্যিক ইমারসন ও হুইটম্যানও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলেন। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে ৫১ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ লন্ডন হয়ে প্রথম আমেরিকা আসেন। লন্ডনে তিনি তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থটি ইংরেজি অনুবাদ ছাপার জন্য দিয়ে আসেন।
রবীন্দ্রনাথ জাহাজে করে নিউইয়র্কে অবতরণ করেন ২৭ অক্টোবর। সঙ্গে ছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। নিউইয়র্ক থেকে তিনি চলে যান ইলিনয় রাজ্যের উরবানা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে রথীন্দ্রনাথ অধ্যয়ন করছিলেন। কবি তখনো নোবেল পুরস্কার পাননি, তাই তখন আমেরিকায় তাঁর পরিচিতিও তেমন ছিলো না। সেবার তাঁর আমেরিকা ভ্রমণ ছিলো তাঁর জন্য খুবই আরামদায়ক।
তিনি বেশ কিছুটা সময় অবসর পেয়েছিলেন। সেবার তিনি আমেরিকায় থাকেন ছয় মাস। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণের আগে নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায়ও সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখা কবিতা, নাটক ও তাঁর আত্মজীবনী আমেরিকার সাহিত্যাঙ্গনে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর সেই সফরের সময় প্রথম মহাযুদ্ধের কারণে ইউরোপে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছিলো।
রবীন্দ্রনাথও তখন পশ্চিমা বিশ্বের সমালোচনামুখর ছিলেন। তাঁর সমালোচনার প্রধান কারণ হলো তিনি মনে করতেন, আমেরিকার পক্ষেই বিশ্বমানবতাকে রক্ষায় এগিয়ে আশা সম্ভব। নিউইয়র্কে তিনি বলেন, ‘আমেরিকার এখন যৌবন এবং পশ্চিমা সভ্যতার ও মানবতার বিকাশ এখানেই ঘটবে।’ তখন তিনি আমেরিকার ২৫টি শহরে বক্তৃতা করেন। একেকটি বক্তৃতার জন্য তিনি ৭০০ থেকে ১০০০ ডলার পেয়েছিলেন।
এই অর্থ তিনি সংগ্রহ করছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর জন্য। ১৯২০-২১ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয়বার আমেরিকার ভ্রমণে যান। সে ভ্রমণে তিনি ব্যর্থতার কবলে পরেছিলেন। আমেরিকা তখন ব্রিটিশের অন্যতম সেরা মিত্র। সেই সময় রবি ঠাকুরের ব্রিটিশবিরোধিতাও তাঁর ভ্রমণ ব্যর্থ হওয়ার একটি অন্যতম কারণ।
তিনি উঠলেন নিউইয়র্কের একটি হোটেলে। কিন্তু কোথাও থেকে কোনো আমন্ত্রণ বা অভ্যর্থনা পেলেন না। এই ভ্রমণে তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হন। নিউইয়র্ক থেকে তিনি যান শিকাগো ও টেক্সাসে। এই ভ্রমণের স্থায়িত্ব ছিলো দুই সপ্তাহ। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে রবি ঠাকুরের চতুর্থবার আমেরিকা ভ্রমণ ছিলো বেশ সংক্ষিপ্ত। এবার তিনি কানাডার ভ্যাঙ্কুভার সীমান্ত দিয়ে আমেরিকা প্রবেশ করেন।
সে সময় সীমান্তে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা তাঁর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেন। নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি লিখতে-পড়তে জানেন কি না! এই ঘটনা তাঁকে খুবই মর্মাহত করে। আর তাই তিনি সেই সফরের নির্ধারিত সব বক্তৃতা বাতিল করেন। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকায় রবি ঠাকুরের ছিলো পঞ্চম ও শেষ ভ্রমণ। এই সময় তিনি রাশিয়া থেকে আমেরিকা আসেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট হুবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
সেবার তাঁর প্রতিটি বক্তৃতা সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়েছিলো। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ ছিলো আমেরিকার ‘গ্রেড ডিপ্রেশন’-এর বছর। ১৯৩০-এর ১৪ ডিসেম্বর নিউইয়র্কের ব্রডওয়েতে তাঁর বিদায় সভায় যে অর্থ সংগৃহীত হয়েছিলো, তা রবীন্দ্রনাথ নিউইয়র্ক সিটির বেকারদের জন্য দান করেন। এ ছাড়া সেই সময় নিউইয়র্ক ও বোস্টনে রবীন্দ্রনাথের আঁকা দুটি ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিলো।
৬৭ দিনব্যাপী শেষ আমেরিকা ভ্রমণের সময় নিউইয়র্ক টাইমস রবি ঠাকুরের ওপর ২১টি রিপোর্ট করে, এর মধ্যে দুটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার এবং রবি ঠাকুরের সঙ্গে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের ঐতিহাসিক ছবি ছাপে। সেবার রবি ঠাকুর বিখ্যাত কারনেগি হলে চার হাজার লোকের উপস্থিতিতে বক্তৃতা দেন, কয়েক হাজার মানুষ ওই অনুষ্ঠানের টিকিট না পেয়ে ফেরত যান। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার বস্তুবাদের একজন কট্টর সমালোচক ছিলেন।
একজন সুনাগরিক যেমন তাঁর দেশের কোনো নীতির সমালোচনা করেন, আমেরিকা সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা ছিলো সে রকম। সমালোচনা করলেও তিনি কখনো আমেরিকার ওপর বিশ্বাস হারাননি। তিনি মনে করতেন, বিশ্বমানবতা প্রতিষ্ঠায় আমেরিকা ভূমিকা রাখতে পারে। তাঁর এই আশা থেকে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন।
১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে রবি ঠাকুরকে সম্মান জানাতে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে নিউইয়র্কের ‘টাইমস স্কয়ারের’ নাম এক দিনের জন্য পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘টেগোর স্কয়ার’। সে সময় নিউইয়র্ক সিটির মেয়র ছিলেন রবার্ট এফ ওয়াগনার। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বারের আমেরিকা ভ্রমণের সময় ইউরোপজুড়ে চলছে প্রথম মহাযুদ্ধ। আমেরিকা সরাসরি এই যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়লেও যুদ্ধের আঁচ টের পাচ্ছে যথেষ্ট।
রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় তখন শোনা গেলো যুদ্ধের বিরোধিতা এবং জাতীয়তাবাদের বিরোধিতাও। জাতীয়তাবাদ বিরোধী রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেনি ইতালি, জাপানের মতো বহু দেশের মানুষ। এমনকি খোদ কলকাতা শহরেও তরুণদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন তার এই মতের জন্য। কিন্তু আমেরিকার মানুষ তার এই বক্তব্যের গুরুত্ব বুঝেছিলেন। আর্বানা ভিলেজের যে গির্জাটিতে প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেটি পড়ে ন্যাশনাল হিস্টোরিক্যাল বিল্ডিং হিসাবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। চানিং-ম্যুরে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় টেগোর ফেস্টিভ্যাল।
ইলিনয় শহরের এবং আশেপাশের সমস্ত বাঙালির কাছে এই উৎসব বছরের শ্রেষ্ঠ উৎসব। আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কবি ও কবিতার কোনও গণভূমিকা প্রায় নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিরা সে দেশে এলে কেউ জানতেই পারেন না। সংবাদপত্র সেসবকে খবর বলেই গণ্য করে না, জনতারও কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু প্রায় একশো বছর আগে ঠিক তেমন ছিলো না। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সফরে তাঁকে নিয়ে যথেষ্ট মাতামাতি করেছিলো সংবাদমাধ্যম।
বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ জানান। রবীন্দ্রনাথের মনে তখন ‘বিশ্বভারতী’ গড়ার স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন সাকার করতে গেলে চাই পাহাড়প্রমাণ অর্থ। প্রতিটি ভাষণের জন্য তাঁকে দেয়া হলো ৭০০ ডলার, একশো বছর আগে, বিশেষ করে আমেরিকার ‘গ্রেট ডিপ্রেশন‘-এর সময়ে যা অচিন্ত্যনীয়।
মিনিয়াপোলিস ট্রিবিউন এই ঘটনা সম্বন্ধে বাঁকা সুরে লিখেছিলো, এর চেয়ে বড়ো কোনো ব্যবসায়ী ভারতবর্ষ থেকে আমাদের এদিকে কখনো আসেননি, এ কথা নিশ্চিত। কী বলছিলেন কবি এইসব ভাষণে? ওর মূল সুর ছিলো এক ভারতীয় সাধকের সুর, যিনি কাব্য, শিল্প, সংগীত ও জীবনে আত্মার প্রগাঢ়তা ও শান্তির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিচ্ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের পাশাপাশি আমেরিকান যুদ্ধনীতি ও জীবনযাত্রারও কড়া সমালোচনা করছিলেন।
লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক